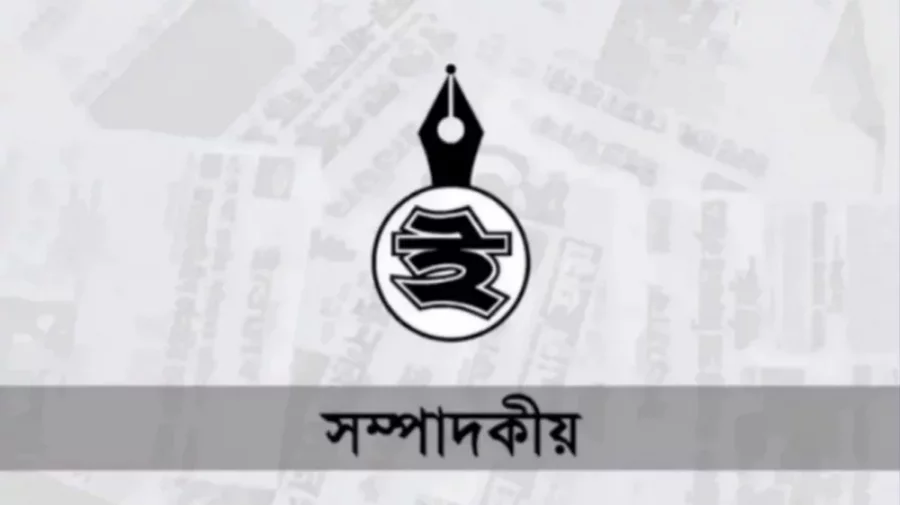সভ্য মানবজগতে মৌলিক অধিকারের তালিকা করিলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সর্বাগ্রে গুরুত্ব পায়। ইহা এক আশ্চর্য অধিকার-যাহা মানবমনে যতখানি স্বাভাবিক, রাষ্ট্রশক্তির নিকট ততখানিই বিরক্তিকর। শাসকের কানে যে কথা মধুর নহে, তাহাই সাধারণ মানুষ উচ্চারণ করিতে চাহে; আর শাসকের প্রথম কাজ হইল সেই বিরক্তিকর বাণীকে দমন করা। অতএব, পৃথিবীর ইতিহাসে ভিন্নমত দমনের বিষয়টি যুগে যুগে ভয়ংকররূপে দেখা গিয়াছে। এই অধিকার অর্জনের জন্য বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে অসংখ্য দার্শনিক, জ্ঞানপিপাসু নাগরিক, কবি-লেখক এমনকি রাজনীতিকও।
মতপ্রকাশের অধিকারের ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করিতে পারি ইংরেজ কবি জন মিল্টনকে। ১৬৪৪ সালে প্রকাশিত ‘এরিওপাজিটিকা: এ স্পিচ ফর দ্য লিবার্টি অব আনলাইসেন্স প্রিন্টিং’-এ তিনি বলেন, ‘আমাকে জানিতে দাও, বলিতে দাও এবং যুক্তি উপস্থাপন করিতে দাও। বিবেকের নির্দেশে মুক্তভাবে বলিবার অধিকারই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা।’ ভাবিলে বিস্ময় জাগে-যেইখানে তখনো লোকে ইচ্ছামতো রক্তপাত করিতে পারিত, সেইখানে ইচ্ছামতো ছাপাখানা ব্যবহার করা ছিল গুরুতর অপরাধ!
অপরদিকে, ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) ছিলেন ভিন্ন রীতির মানুষ। তিনি অন্যের বক্তব্যে একমত হউন বা না হউন, সেই বক্তব্য উচ্চারণের অধিকারকে মৃত্যুপণ করিয়া রক্ষা করিবার অঙ্গীকার দিতেন। যদিও বিখ্যাত উক্তিটি তাহার নিজস্ব কলম হইতে নহে-এভলিন বিট্রিস হল নামক জীবনীকার তাহার চেতনার সারমর্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন- ‘আমি তোমার কথায় একমত নহি; কিন্তু মৃত্যুপণ করিয়া তোমার বলিবার অধিকার রক্ষা করিব।’ জন স্টুয়ার্ট মিল অবশ্য এই আলোচনায় যুক্ত করিলেন এক দার্শনিক বিশ্লেষণ। ‘অন লিবার্টি’ (১৮৫৯) গ্রন্থে তিনি বলিলেন- ‘চিন্তার স্বাধীনতা এবং তাহা প্রকাশের স্বাধীনতা একই সূত্রে বাঁধা; একটিকে দমন করিলে অপরটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মরিয়া যায়।’ মিলের এই তত্ত্ব আমাদের সতর্ক করিয়া দেয়, সত্যের সম্ভাবনা কখনো একপাক্ষিক নহে। যেই মতামত আমাদের নিকট ভুল বলিয়া মনে হইতে পারে, সেই মতামতের মধ্যেই ভবিষ্যতের কোনো সত্যের বীজ লুকাইয়া থাকিতে পারে। অতএব ভিন্নমতকে রুদ্ধ করা মানে সেই সত্যের বীজটিকে আগেভাগে দাফন করা।
মতপ্রকাশের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এখন বিশ্বের দেশে দেশে গৃহীত হইয়াছে বা হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭৯১ সালে প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে ঘোষণা করিয়াছে-কোনো আইন মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে পারিবে না। এই আইনি ঢাল কেবল শব্দসজ্জা নহে; আদালতের রায়ে ইহা বহু বার কার্যকর হইয়াছে। যেমন-১৯৬৪ সালে আলাবামা অঙ্গরাজ্যের এক পুলিশ কমিশনার ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনেন। সুপ্রিম কোর্ট রায়ে জানাইল-গণপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বিষয়ে সংবাদ প্রকাশে কেবল ভুল বলিলেই চলিবে না, বরং ‘ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচারের প্রমাণ’ আবশ্যক। এই রায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আমেরিকায় প্রায় অটল ভিত্তি প্রদান করে। সংবাদমাধ্যমের জন্য ইহা একপ্রকার স্বর্ণের চাবিকাঠি, যাহা শাসকশ্রেণির তিক্ত সমালোচনাকেও বৈধ করিয়া দেয়।
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সবচাইতে সুন্দর দিকটি হইল, পাড়ার চায়ের দোকানে একদল হয়তো বলিল, ‘দেশ সর্বনাশের পথে’, তেমনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবার অন্য দল ঘোষণা করিল-‘দেশ এখন পৃথিবীর সেরা।’ উভয় পক্ষই ভুল হইতে পারে, আবার উভয় পক্ষই আংশিক সত্য বলিতে পারে; কিন্তু এই বিরোধিতার মধ্যেই গণতন্ত্রের প্রাণরস লুকাইয়া রহিয়াছে। যদি একদিন সকলে একই ভাষ্যে, এক সুরে কথা বলে-তাহা হইলে বুঝিতে হইবে-স্বাধীনতার প্রাণভোমরা কোথাও না কোথাও আটকা পড়িয়া গিয়াছে।
সুতরাং, আমাদেরও শিখিতে হইবে-মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেবল আমার নিজের পক্ষ নহে, শত্রুর পক্ষও রক্ষা করিতে হয়। কারণ, আজ যাহার কণ্ঠরোধ হইল, কাল তাহার স্থলে আমার কণ্ঠরোধ হইতেও পারে। অন্যের মুখের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার মধ্যেই নিজের কণ্ঠস্বর টিকাইবার আশ্বাস নিহিত। আর ইহাও স্মরণে রাখা ভালো- ‘নীরবতা’ অনেক সময় শান্তি আনে বটে; কিন্তু সেই শান্তি আসলে শ্মশানের শান্তি।ইত্তেফাক/এএম